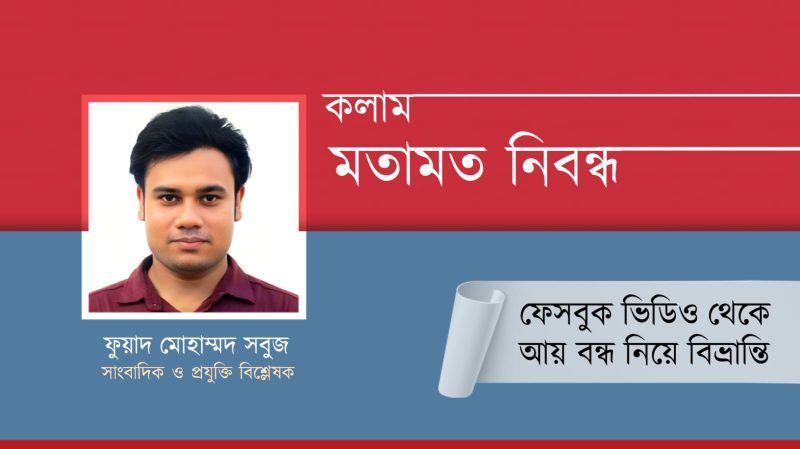
গত কয়েকদিন ধরে দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে যে, ফেসবুক ভিডিও থেকে আয় করার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। এই সংবাদটি ফেসবুকের নতুন কনটেন্ট কাঠামো এবং প্রযুক্তিগত বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি অসঙ্গতিপূর্ণ। একজন প্রযুক্তি বিশ্লেষক হিসেবে বলতে পারি, ফেসবুক এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি যা ভিডিও নির্মাতাদের আয় বন্ধ করে দেবে। বরং ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে কোম্পানিটি তাদের ভিডিও এবং রিলসকে একটি একীভূত প্ল্যাটফর্মে (Unified Platform) নিয়ে এসেছে, যার ফলে ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট খুঁজে পাওয়া ও উপভোগ করা আরও সহজ ও গতিশীল হয়েছে।
মূলত, ফেসবুক এখন শর্ট-ফর্ম (রিলস) এবং লং-ফর্ম (ভিডিও) কনটেন্টকে একটি অভিন্ন ‘ভিডিও’ ট্যাবের অধীনে একত্রে উপস্থাপন করছে। এটি মেটা-র কনটেন্ট উপভোগের মডেল (Content Consumption Model) পুনর্গঠনের একটি অংশ। ভিডিওর উপস্থাপনার ধরন বদলালেও এর মনিটাইজেশন ব্যবস্থা (Monetization Module) অপরিবর্তিত রয়েছে। ইন-স্ট্রিম অ্যাড, ফ্যান সাবস্ক্রিপশন, ব্র্যান্ডেড কনটেন্টসহ আয়ের সব পথ আগের মতোই কার্যকর আছে। অনেকেই ভিডিও ফিডের এই পরিবর্তনকে ভুলবশত “মনিটাইজেশন বন্ধ” হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন, যদিও এটি কেবল ইউজার ইন্টারফেস (UI) এবং ইউজার এক্সপেরিয়েন্স (UX) স্তরের একটি একত্রীকরণ মাত্র। প্রযুক্তিগতভাবে, এটি কোনো সুবিধা বাতিল করা নয়, বরং একটি কেন্দ্রীভূত উন্নয়ন।
ফেসবুকের বিজ্ঞাপন সরবরাহ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এনগেজমেন্ট-ভিত্তিক আয়ের মডেল। একজন ব্যবহারকারী যখন কোনো ভিডিওতে মন্তব্য করেন, লাইক দেন বা শেয়ার করেন, তখন সেই কনটেন্টের অ্যালগরিদমিক প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ফলে সেখানে ইন-স্ট্রিম অ্যাড প্রদর্শনের হার বাড়ে এবং বিজ্ঞাপনদাতারা সেই সুযোগের জন্য অর্থ পরিশোধ করেন। নির্মাতারা এভাবেই আয় করেন। এছাড়া, ভিডিওর বিবরণে থাকা কোনো ওয়েবসাইটের লিংকে ক্লিক করা হলে সেই ওয়েবপেজের অ্যাড নেটওয়ার্ক থেকেও নির্মাতার আয় হতে পারে। সুতরাং, ফেসবুক মনিটাইজেশন হলো একটি বহুস্তরবিশিষ্ট বিজ্ঞাপন কাঠামো, যা এখনো পূর্ণ কার্যক্রমে সচল।
এই বিভ্রান্তির মূল কারণ হলো তথ্যভিত্তিক সাংবাদিকতার ঘাটতি এবং ক্লিকবেইট সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ। অনেক সংবাদমাধ্যম মেটার অফিশিয়াল নিউজরুম, হেল্প সেন্টার বা Meta for Creators ড্যাশবোর্ডের ঘোষণাগুলো যাচাই না করেই ইউটিউব, টিকটক বা অন্যান্য কনটেন্ট নির্মাতাদের অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করছে। প্রযুক্তিনির্ভর যেকোনো পরিবর্তনকে ঢালাওভাবে ‘আয় বন্ধ’ বলার এই প্রবণতা সাধারণ ব্যবহারকারী ও নির্মাতাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। অথচ ফেসবুক কোনো ফিচার সরিয়ে দিলে তা সব সময় পূর্বঘোষণা, ড্যাশবোর্ড নোটিফিকেশন এবং অফিশিয়াল ব্লগের মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে জানিয়ে থাকে।
কনটেন্ট নির্মাতাদের উচিত তাদের ড্যাশবোর্ডের ‘ইনসাইটস’ (Insights) ও ‘অ্যাডস ম্যানেজার’ (Ads Manager) নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে আয়ের উৎসগুলো বিশ্লেষণ করা। ড্যাশবোর্ডে গেলেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, ভিডিও ভিউ, সিপিএম (CPM), সিটিআর (CTR) এবং আনুমানিক উপার্জনসহ সব তথ্য আগের মতোই প্রদর্শিত হচ্ছে। ফিচারের এই একত্রীকরণ হয়তো ইউজার ইন্টারফেস ও অ্যালগরিদমে সামান্য পরিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু আয়ের অর্থনৈতিক কাঠামোটি অপরিবর্তিত রয়েছে। এ কারণে, প্রযুক্তিগত দিক না বুঝে যেকোনো আপডেটকে নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা কেবল ভুলই নয়, দায়িত্বজ্ঞানহীনতারও পরিচায়ক। আর এই দায় শুধু সংবাদমাধ্যমের নয়, কনটেন্ট নির্মাতাদেরও এ বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি।
সার্বিকভাবে, ফেসবুক ভিডিও থেকে আয় বন্ধ হয়ে গেছে—এই ধারণাটি একটি গুজব বা ভুল ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফেসবুক মূলত কনটেন্ট পরিবেশন এবং ব্যবহারকারীর এনগেজমেন্ট আরও কার্যকর করতে প্রতিনিয়ত সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করছে। এই একীভূত ভিডিও প্ল্যাটফর্মের ফলে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত হবে এবং নির্মাতাদের জন্য কনটেন্ট বণ্টন ও রিচ বাড়ানো আরও সহজ হবে। একজন প্রযুক্তি বিশ্লেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই পরিবর্তনটি ফেসবুকের উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ, কোনো কিছু বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নয়। তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণই পারে গুজবকে প্রতিহত করতে এবং ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে।
লেখক : প্রযুক্তি বিশ্লেষক; শিক্ষার্থী, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস।
