
সবকিছুর পরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, যা হলো বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চীন থেকে বাংলাদেশে আমদানি হয় প্রায় ২ লাখ ৯১ হাজার ৬৬১ কোটি টাকার (প্রায় ২ হাজার ৪২৮ কোটি মার্কিন ডলার) পণ্য, বিপরীতে বাংলাদেশ চীনে রপ্তানি করেছে মাত্র ৯ হাজার ১৫১ কোটি টাকার (প্রায় ৭৬ কোটি ডলার) মতো পণ্য। অর্থাৎ, বাণিজ্য ঘাটতি এখনও ব্যাপক।
আশার কথা হলো, চীন বাংলাদেশকে ৯৮ শতাংশ পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু তারপরও রপ্তানি বাড়ছে না কেন?
চীন-বাংলাদেশ বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত বিশ্লেষকরা বলছেন, এই বাধা শুল্কের নয়, এই বাধা ‘সাংস্কৃতিক’। তাঁদের মতে, বাংলাদেশি রপ্তানিকারকরা প্রায়শই চীনের বিশাল বাজারের ভোক্তাদের রুচি, পছন্দ, রঙ বা প্যাকেজিংয়ের ধরন ধরতে পারছেন না।
তবে চীন বিশেষজ্ঞ এবং দীর্ঘদিনের ব্যবসায়ীদের মতে, দ্বিতীয় এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধাটি হলো চীনের ব্যবসায়িক সংস্কৃতির মূল ধারণা ‘গুয়ানশি’ সম্পর্কে অজ্ঞতা। তাঁরা ব্যাখ্যা করেন, ‘গুয়ানশি’-এর আভিধানিক অর্থ ‘সম্পর্ক’ হলেও এর ব্যবসায়িক প্রয়োগ আরও গভীর। চীনে ব্যবসায়িক চুক্তি শুধু সেরা মূল্য বা পণ্যের মানের ওপর নির্ভর করে না; এটি নির্ভর করে দীর্ঘমেয়াদী ব্যক্তিগত আস্থা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সম্পর্কের ওপর।
চট্টগ্রামের একজন সফল চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিকারক নজরুল ইসলাম জানান, “প্রথম দুই বছর আমি শুধু ইমেইল পাঠিয়ে এবং স্যাম্পল কুরিয়ার করেই ব্যর্থ হয়েছি। যখন আমি নিজে চীনে গেলাম, তাদের সাথে খাবার খেলাম, ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করলাম (গুয়ানশি) এবং তাদের সংস্কৃতিকে সম্মান দেখাতে শুরু করলাম, কেবল তখনই ব্যবসার দরজা খুলল।”
‘সফট পাওয়ার’ বনাম ‘হার্ড কালচার’
যখন ‘সাংস্কৃতিক বিনিময়’-এর কথা ওঠে, তখন আমাদের চোখে ভাসে জমকালো চীনা নববর্ষের উৎসব, অ্যাক্রোব্যাটদের মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনী কিংবা কোনো চলচ্চিত্র উৎসবের দৃশ্য। এগুলো ‘সফট পাওয়ার’-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তা অবশ্যই দুই দেশের মানুষকে কাছাকাছি আনে।
কিন্তু চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে গত দশকে চীনের সবচেয়ে শক্তিশালী ‘সাংস্কৃতিক বার্তা’টি এসেছে ভিন্ন পথে। সেটি হলো চীনের ‘হার্ড কালচার’ বা কাজের সংস্কৃতি—তাদের প্রকৌশলগত দক্ষতা, বিস্ময়কর সময়নিষ্ঠা এবং অসাধ্য সাধনের সক্ষমতা।
কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে যখন টানেল নির্মিত হয়, কিংবা মিরসরাইয়ের বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে যখন একের পর এক চীনা বিনিয়োগে শিল্প স্থাপন হয়, তখন তা শুধু একটি অবকাঠামো থাকে না। এটি চীনের সক্ষমতা, কর্মনিষ্ঠা এবং প্রতিশ্রুতির একটি জীবন্ত বিজ্ঞাপনে পরিণত হয়। এই বিনিয়োগ এখন আর শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই।
বেপজার তথ্য অনুযায়ী, চীন বর্তমানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগকারী দেশ। উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রাম ইপিজেডে চীনা মালিকানাধীন ‘ডিরেকশন টেকনোলজি (বাংলাদেশ) লিমিটেড’ ৩০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে একটি হেডফোন ও ডেটা ক্যাবল উৎপাদন কারখানা স্থাপন করছে, যেখানে প্রায় ৪৭৮ জন স্থানীয় কর্মীর কর্মসংস্থান হবে। একইভাবে, আনোয়ারার চায়না ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে ‘চায়না লেসো গ্রুপ’ ৩২.৭৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে কারখানা স্থাপন করছে, যা ৫০০-৬০০ জনের নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করবে।
চীনা পণ্যের আমদানিকারক চট্টগ্রামের চকবাজারের ব্যবসায়ী মো. মোফাচ্ছল যেমনটা বলছিলেন, “একটি নৃত্য পরিবেশনা দেখা অবশ্যই আনন্দের। কিন্তু যখন আমি দেখি একটি চীনা কোম্পানি অসম্ভবকে সম্ভব করে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণ করছে, তখনই আমি তাদের উৎপাদন সক্ষমতার ওপর সত্যিকারের আস্থা পাই। এই আস্থার কারণেই আমি নির্দ্বিধায় কোটি টাকার চীনা মেশিনারিজ আমদানির চুক্তি করতে পারি।”
এই ‘হার্ড কালচার’ বা সক্ষমতার সংস্কৃতিই দুই দেশের বাণিজ্যের সেই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে, যার ওপর দাঁড়িয়ে সফট পাওয়ার বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিনিময় আরও সহজ হয়েছে।
বাণিজ্যের প্রয়োজনে সংস্কৃতি: উল্টো স্রোতের গল্প
প্রচলিত ধারণা হলো, সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া ভালো হলে বাণিজ্য বাড়ে। কিন্তু চীন-বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চট্টগ্রামে, আমরা একটি উল্টো এবং আরও শক্তিশালী প্রবণতা লক্ষ্য করছি। এখানে, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য এবং বিশাল অবকাঠামো প্রকল্পগুলোই একটি ‘প্রয়োজনভিত্তিক’ বা ‘বাধ্যতামূলক’ সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করছে।
এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ভাষা। (যেমনটি আমরা এই ধারাবাহিকের প্রথম প্রতিবেদনে দেখেছি) চট্টগ্রামের হাজার হাজার তরুণ-তরুণী আজ চীনা ভাষা শিখছেন শুধু শিক্ষাবৃত্তির জন্য নয়, বরং সিইপিজেড, কেইপিজেড, কর্ণফুলী টানেল বা মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে একটি ভালো বেতনের চাকরির আশায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ‘অপেক্ষমান তালিকা’ই প্রমাণ করে—চাহিদাটি তৈরি করেছে অর্থনীতি।
একই ঘটনা ঘটছে প্রকল্প এলাকাগুলোতে। আনোয়ারা, মিরসরাই বা সিইপিজেড-এর আশেপাশের এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সেখানে বাজারের প্রয়োজনেই ছোট ছোট ‘সাংস্কৃতিক হাব’ গড়ে উঠেছে। চীনা প্রকৌশলী ও কর্মীদের চাহিদা মেটাতে স্থানীয় উদ্যোক্তারা চালু করছেন খাঁটি চীনা রেস্তোরাঁ, চাইনিজ গ্রোসারি শপ, এমনকি সেলুন। এটি কোনো রাষ্ট্রীয় আয়োজন নয়, এটি বাজারের প্রয়োজনে তৈরি হওয়া একটি স্বতঃস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন।
পণ্যের পরিচিতি: ‘মেইড ইন চায়না’ থেকে ‘ব্র্যান্ড চায়না’
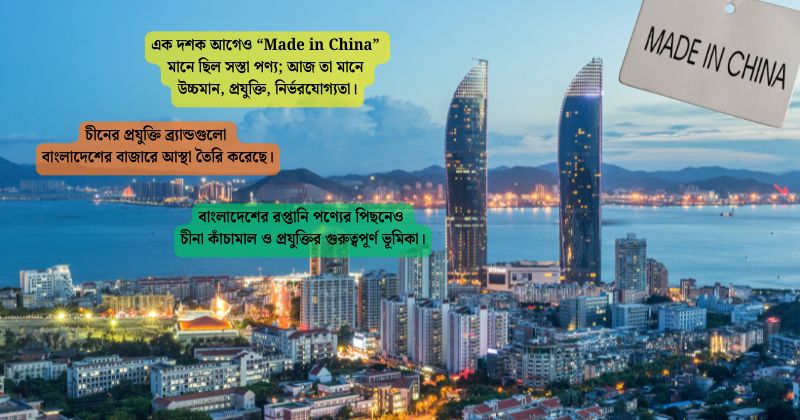
সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের আরেকটি বড় সাফল্য হলো ‘মেইড ইন চায়না’ ট্যাগটির ধারণাগত পরিবর্তন। এক দশক আগেও চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ বা রিয়াজউদ্দিন বাজারের ব্যবসায়ীদের কাছে এই ট্যাগটি সস্তা বা কম মানসম্পন্ন পণ্যের প্রতীক ছিল। কিন্তু আজ সেই ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এই বদলের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে চীনের প্রযুক্তি ব্র্যান্ডগুলো।
তবে এই সম্পর্ক আরও গভীর। বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সাবেক মহাসচিব আল মামুন মৃধা যেমনটা ব্যাখ্যা করেন, “বাংলাদেশের পণ্য সরাসরি চীনে রপ্তানি কম হলেও আমরা সারা পৃথিবীতে যে পণ্য রপ্তানি করি, তার বেশিরভাগের পেছনে চীনের অবদান উল্লেখযোগ্য। দেশের উদ্যোক্তারা চীন থেকে কাঁচামাল আমদানি করে তাতে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে নানা দেশে রপ্তানি করছেন।”
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমানও এই প্রবণতা স্বীকার করে বলেন, “আগে মূলধনি যন্ত্রপাতি প্রধানত জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আসতো। এখন সেই জায়গা দখল করেছে চীন।”
এই ‘ব্র্যান্ড চায়না’র ধারণা চীনের অন্যান্য পণ্যের জন্যও চট্টগ্রামের রিয়াজউদ্দিন বাজার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এর পাশাপাশি, প্রতি বছর হাজার হাজার বাংলাদেশি ব্যবসায়ী যখন চীনের গুয়াংজুতে ‘ক্যান্টন ফেয়ার’-এর মতো বিশাল বাণিজ্য মেলায় অংশ নিচ্ছেন, তখন তারা সরাসরি চীনের উৎপাদন সক্ষমতা, শৃঙ্খলা এবং বৈচিত্র্য দেখছেন। এই সরাসরি অভিজ্ঞতা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেকোনো দ্বিধা দূর করে দিচ্ছে।
তবে এই ভারসাম্যহীনতা এবং ঋণের বিষয়ে সতর্ক করেছেন খোদ অর্থনীতিবিদরাও। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেনের মতে, “চীনের বিনিয়োগ বাংলাদেশের অবকাঠামো ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে ঋণের শর্ত ও প্রকল্পগুলোর টেকসইতা নিশ্চিত করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ।”
অবকাঠামো ‘হার্ডওয়্যার’, বোঝাপড়াই ‘সফটওয়্যার’
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের একটি কোলাহলপূর্ণ সাইট। একটি নতুন ইস্পাত কারখানার ভারী যন্ত্রপাতি স্থাপন চলছে। মধ্যাহ্নের তপ্ত রোদ উপেক্ষা করে একটি জটিল ক্রেন-অপারেশনের নকশা নিয়ে ঝুঁকে আছেন চীনা প্রকৌশলী চেন এবং বাংলাদেশি প্রজেক্ট ম্যানেজার আমিনুল হক।
আমিনুল হক, চট্টগ্রামেরই সন্তান, একটি সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে দ্রুত একটি বিকল্প অ্যালাইনমেন্ট আঁকলেন। মিস্টার চেন সেটি দেখলেন, কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর সশব্দে হেসে মাথা নাড়লেন। ভাষার অনুবাদ ছাড়াই, অভিজ্ঞতার এক অভিন্ন ভাষায় তারা একটি জটিল প্রকৌশলগত সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। এরপর আমিনুলের বাড়িয়ে দেওয়া এক কাপ চায়ে চুমুক দিতে দিতে চেন তার কাঁধ চাপড়ে দিলেন।
এই একটি দৃশ্যই চীন-বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের গভীরতম চিত্র। এই সম্পর্ক শুধু ডলার, ইউয়ান বা কন্টেইনারের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। এর ভিত্তি তৈরি হচ্ছে প্রতিদিনের এই মানবিক মিথস্ক্রিয়া, সমস্যা সমাধান এবং ঘাম-মেশানো চায়ের কাপে অর্জিত পারষ্পরিক আস্থার ওপর।
চীন-বাংলাদেশ বাণিজ্য নিয়ে গবেষণা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, “চীন-বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে যদি একটি সুপার হাইওয়ে ধরা হয়, তবে কর্ণফুলী টানেল, মিরসরাই শিল্পনগর, বন্দর এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো হলো সেই হাইওয়ের ‘হার্ডওয়্যার’। এগুলো দৃশ্যমান এবং অপরিহার্য।”
তিনি আরও বলেন, “কিন্তু কোনো ‘হার্ডওয়্যার’ সচল রাখার জন্য প্রয়োজন ‘সফটওয়্যার’-এর। আর এই সম্পর্কের সফটওয়্যার হলো সাংস্কৃতিক বিনিময়। এই সফটওয়্যার হলো মিস্টার হুয়াং ও রহমান সাহেবের সেই আস্থার মুহূর্ত, ক্যান্টন ফেয়ারে অর্জিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং ‘গুয়ানশি’র মতো গভীর সাংস্কৃতিক ধারণাকে সম্মান করা।”
এই বিশেষজ্ঞ মনে করেন, “‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ’ বা অর্থনৈতিক করিডোরগুলো হলো কাঠামো। আর এই সাংস্কৃতিক বোঝাপড়াই হলো সেই মানবিক ভিত্তি, যা এই কাঠামোকে সচল, টেকসই এবং দুই দেশের জন্য সত্যিকার অর্থেই লাভজনক করে তুলছে। এটিই দুই দেশের বন্ধুত্বের সত্যিকারের সেতুবন্ধন।”
আগামীকাল পড়ুন: যেভাবে ‘সভ্যতার সহযাত্রী’ হচ্ছে চীন